অলোকের ঝর্নাধারায়
(আমার টুকরো জীবন)
পর্ব-৩
প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে আমার মামারবাড়ি মধ্যবিত্ত হলেও খাওয়াপরায় কখনও কোনও অভাব দেখিনি। আমার ছেলেবেলার অনেকটা এবং পরেও যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখনও অন্তত গ্রীষ্মের ও পুজোর ছুটিটা কলকাতার-৬, জোড়াসাঁকোর ৫৯ নং বলরাম দে স্ট্রীটে আমার কাটতো বেশিরভাগ। সেখানে ভাগ্নাভাগ্নির সমস্ত আদর-যত্ন আমি একাই ভোগ করেছি। মামাতো ও মাসতুতো ভাইরা তখনও জন্মগ্রহণ করেনি এবং আমার নিজের ভাইবোনেরাও খুব কম গিয়ে থেকেছে । আমি সেখানে একাই রাজা ছিলাম। একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত নিজের একটা রাজত্ব ছিল। তবে মামা মাসিদের শাসন ছিল খুব। আমার বড় মাসিমা ১৪ বছর বেলায় বিধবা হয়ে চিরকাল মামার বাড়ি ছিলেন শুনেছি মাত্র একবছর তাঁর দাম্পত্য জীবন কেটেছিল। হাওড়ার শিবপুরে তখন পাল ফার্মেসীর ওষুধের দোকান মানে বিশাল টাকা পয়সা, বেশ ধনী পরিবার। তখনকার দিনে শিবপুরের গন্ধবণিক ওই পরিবারের ছেলের যে টিবি ছিল এটাও খুব আশ্চর্যের। ওদের কাছ থেকে মাসিমার মাসোহারা পেতে অনেক কোর্টঘর করে পাওয়া গিয়েছিল মাসে ১৯/২০ টাকার মতো। কারণ ওদের ওষুধের দোকানটি ছিল সারা জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান এবং আইনত আমার মাসিমার চার আনা শেয়ার ছিল প্রচুর জায়গা জমিও ছিল কিন্তু আমার মাসিমা ওই টাকাটা ছাড়া আর কিছুই পেতেন না। আমি যখন যেতাম, মাসিমা সেখান থেকে আমাকে তখন রোজ সকালে ২ টো জিলিপির পয়সা দিতো। মামার বাড়িতে সকালে কিন্তু ফিরপো কোম্পানীর পাঁউরুটি দেড় পাউন্ড সঙ্গে আমার বড়মামা আনতো কাঁচের বোতলের হরিণঘাটার দূধ। ছোট থেকেই চা খাওয়ার বায়না ছিল আমার। মামার বাড়িতে একপিস পাঁউরুটি কলাইয়ের গ্লাসে চা। ( কলকাতায় নিত্য প্রয়োজনে কলাইয়ের বাসন ব্যবহার হোতো) তারপর একছুটে দু একটা সরু গলির ভেতর দিয় দে ছুট মামার বাড়ির একেবারে পেছন দিকে। নোপানী স্কুলের ভেতর দিয়ে সতীমায়ের মন্দির হয়ে সুন্দর চন্দনের গন্ধ ও পুজোর ঘন্টার আওয়াজ আর স্কুলের দারোয়ানের ফাঁক গলে বিখ্যাত রামবাগানে। ওখানে হিন্দুস্তানীদের দোকানে ঝুরিভাজা,জিলিপি সিঙাড়া খুব বিক্রি হতো। উত্তর কলকাতা মানে গায়ের ওপর গায়ে বাড়ি। চোর একটা ছাদে উঠতে পারলে আর রক্ষা নাই, দশটা বাড়ি গায়ে গায়ে। তাই কোনও ভাবেই কোনও বাড়ির সামনেটা ছাড়া তিনদিকে দেখা যেতনা। সতীমায়ের মন্দির স্কুলের একতলায়। বড় মাসিমা পই পই করে বলে দিত, দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলো ডাকলে একদম যাবিনা। সাজাগোজা ঘরে ঘরে মেয়েরা কেন, সাত সকালে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কিছুতেই মাথায় ঢুকতো না। এখন ভাবি ওইটুকু ছেলেকেই বা ওরা কেন ডাকবে! আসলে মাসিমার ভয় করতো আমি যেন হারিয়ে না যাই। ওই জিলিপির দোকান থেকেই বেশ্যাপাড়ার শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তখন থেকেই বাঙালিরা ক্রমশ ওইসব জায়গায় কোনঠাসা হয়ে পড়ছিল। একচেটিয়া মাড়োয়াড়ি পাড়া হয়ে উঠছিল। এখন তো বাঙালি দুচার ঘর আছে। মামার বাড়িতে মজার একটা জিনিস ছিল সেটা হলো উত্তর কলকাতার ওই ঘিঞ্জি বাড়িগুলিতে একতলায় আলো আসার জন্যে উঠোনের মাথায় দোতালার মেঝেতে কিছুটা জায়গা চৌকোনো ফাঁকা রেখে বড় বড় লোহার রড মেঝেতে গাঁথা থাকতো। কোনও কোনও হিন্দি সিনেমায় এইরকম বাড়িঘরের পরিবেশ আমরা দেখেছি। বেশ মজার এই জন্য আমরা ওর ওপর সাবধানে দাঁড়িয়ে বসে নীচটা সম্পূর্ণ দেখতে পেতাম। আবার মাসিরা অনেকে জড় হলে ওখানে উপুড় হয়ে দোতলায় শুয়ে একতলার লোকেদের সঙ্গে গল্প করতে পারতো। রডগুলো লম্বা ও চওড়া দিকে মেঝেতে পেতে চতুর্দিকে মেঝের ভেতর গাঁথা থাকতো। এমনকি টাকা পয়সা বই টুকটাক জিনিস ওপর থেকে নীচে মামিয়ে দেওয়া যেত। নীচ থেকে তোলার জন্যে একটা দড়িতে একটা আঁকশি ঝুলতো। খবর কাগজ বেঁধে দোতালায় তুলে নিয়েছি কতবার। আর সিঁড়িগুলোর সাইজ ছিল ছোট ছোট তিনতলা পর্যন্ত। উঠোনের পাশে বিশাল চৌবাচ্চায় জল উপচে পড়তো। দিদিমা মুখে দোক্তা নিয়ে সকাল ছটা থেকে রান্নায় বসতো দুবেলার রান্না করে উঠতো সেই দুটোয়। সে রান্না কোনও শেফের দ্বারাও সম্ভব ছিলনা এত তার স্বাদ। মাটির হাঁড়িতে ভাত হতো। শাকের ঘন্টটায় ঘরের পোস্তর বড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া থাকতো। শেষে বিশ্বেশ্বর ঘি দিয়ে নামানো। মাছের তেলঝাল। একটা কপি বা পটলের তরকারি, আলু বেগুন ভাজা। ভাজা মুগের লাউ দিয়ে ডাল। প্রতিদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই মেনু। রাতে গরমজলে মাখা রুটি নয়তো বিশ্বেশ্বর ঘিয়ের গরম গরম লুচি ছোলার ডাল নারকেল দিয়ে নয়তো ফুলকপি/ ধোঁকার ডানলা বেগুন ভাজা ছোলা দিয়ে কুমড়োর ডানলা। লুচি ছাড়া সমস্ত রান্না দিদিমা একা করতো সকালে। জোগাড় দিত ছোট ও বড় মাসি।
আমার ছোটমাসির কুটনো কোটার শুনেছি শ্বশুরবাড়িতেও তারিফ হতো। অনেক বড় হয়ে মামার বাড়িতে মাংস ডিম ঢুকেছে, মুরগীর মাংস দিদিমা কখনও রাঁধেনি। আর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি। ঠিক ওখানটাতে বসে আমার কথা হোতো দিদিমার সঙ্গে। মামা বাড়ির দাদুর ছিল মান্টেলসের হোলসেল ব্যবসা। তবে আমি দাদুকে দেখিনি। দাদু বড়বাজারে মাল দিয়ে আসতো আর তাগাদায় যেত এছাড়া আর তেমন কাজ নেই শুনেছি দাদু খুব কম বয়সেই ৬০ হওয়ার অনেক আগেই মারা যান। ওই সময়েই ব্যবসায় এত আয় করেছিলেন যে মৃত্যুর পরও সেই সুদের পয়সায় আরও ভালোভাবে ২০ বছর মামাদের চলে যেত। বেঁচে থাকতে এক বড়লোক বন্ধুকে বিশাল অঙ্কের টাকা ধার দেন। সেকথা পরে বলবো। ছোটমামা তখন ডাক্তারি পড়ে ও বড়মামার ম্যানেনজাইটিস হয়ে শরীরের এক দিকটা সম্পূর্ণ পড়ে যায়। বিধানচন্দ্র রায়কে দেখানো হয়েছিল। উনি বলেছিলেন ব্রেন অপারেশন করলে ভালো হয়ে যাবে। বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে অ্যাপয়ন্টমেন্ট নেওয়া হয়েছে। যখন মাত্র ১২০/- টাকায় মামাদের সংসার চলে যেত তখন বিধানচন্দ্র রায়কে স্পেশালভাবে দেখাতে চাইলে উনি নিতেন ৬৪/- টাকা। দেখাতে আমার দুইমাসি ও ছোটমামা ও দাদুর এক বন্ধু গেছেন। আমার মামাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিধানচন্দ্র রায় দূর থেকে বলে দিলেন ব্রেন অপারেশন করলে ঠিক হয়ে যাবে। এই ছিলেন বিধান চন্দ্র রায়ের দূরদৃষ্টি। যাইহোক, ভয়েতে আমার দিদিমা ব্রেন অপারেশনে রাজি হলেন না। আমার বড়মামা ওইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দোতলা বাস, ট্রামে লাঠি নিয়ে যাতায়াত করতেন কষ্টকরভাবে। বড় মামার শখ ছিল ছবি তোলো। বড় বড় দুতিনটে কাঠের বক্স ক্যামেরা ছিল। যাকে দাঁড় করাবার তিনটি অ্যাডজাস্টেবল পায়া ছিল। ক্যামেরায় কালো কাপড় চাপা দিয়ে প্লেট ভরে ছবি তোলা হোতো। লেন্সের ঢাকনা কতক্ষণ খুলে রাখলে কতটা আলো ছবি নেবে ছবি তুলে তুলে তা পরীক্ষা করে প্র্যাকটিস করে বুঝে নিতে হোতো। ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করে কালো ঢাকা দেওয়া বাক্সো থেকে নিমিষে বার করে ক্যামেরায় লাগাতে হোতো কালো কাপড় ঢেকে। বাড়িতেই সে কারণে স্টুডিও ডার্করুম করতে হয়েছিল। মেটাল কেমিকেল, ফিল্ম, ব্রোমাইড, সলিউশন, পেপার সব সাজানো থাকতো। ডার্করুমে লাল আলো জ্বলতো। ছবি উঠতো শুধুমাত্র বাড়ির লোকেদের। বাইরের জন্য ছিল একটা ছোট হ্যান্ডি বিলিতি ডবল লেন্সের আগফা কালো রঙের ক্যামেরাও। ভূবনেশ্বরে মামাদের বাড়ি মধুপুরে দাদুর বন্ধুর বাড়িতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাওয়া হোতো। (ক্রমশ)

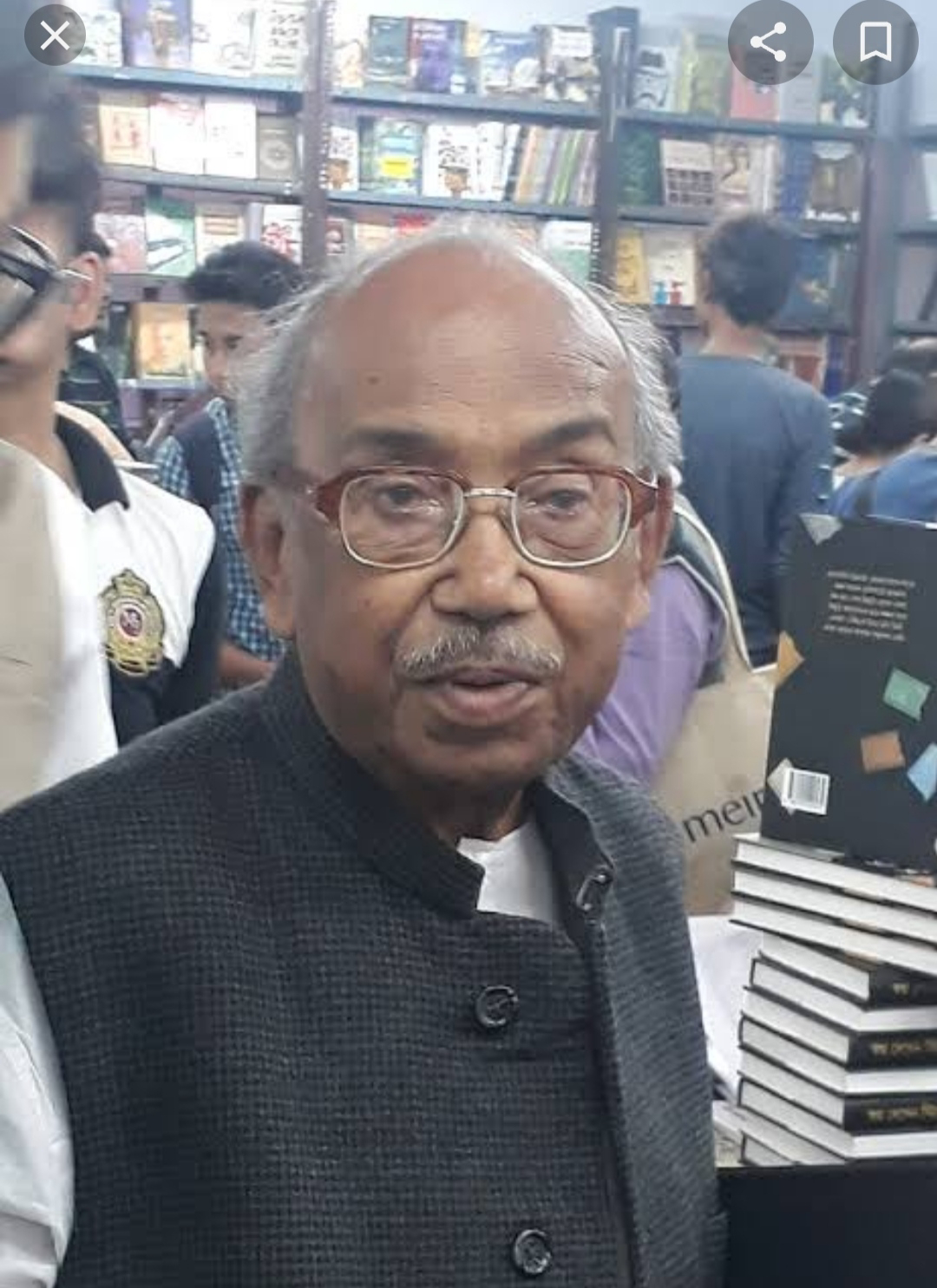

কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন